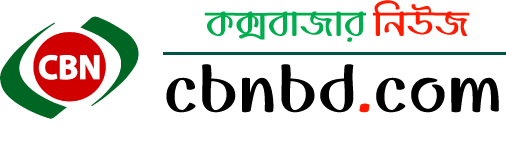জালাল আহমদ :
কোটা সংস্কার আন্দোলন গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে শাসকের বিরুদ্ধে রাজপথে দাঁড়িয়ে অধিকার আদায়ের একটা সফল ইতিহাস এবং
অনুপ্রেরণার উৎস। ক্ষমতাসীন দলের এবং সরকার দমন- পীড়ন,মামলা- হামলা, জেল -জুলুম চালিয়েও
এই আন্দোলন ভন্ডুল করতে পারে নি।দেশী এবং বিদেশী শক্তির চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অধিকাংশ সহযোদ্ধারাই পরবর্তী সময়ে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি আলোচিত আন্দোলন। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাইরেও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের লড়াই করা যায়। তার অন্যতম উদাহরণ ২০১৮ সালের এই দুইটি আন্দোলন।
কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট:
বাংলাদেশের সরকারী চাকুরীতে কোটা পদ্ধতি ছিল মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ফাঁদ। একজন শিক্ষার্থী প্রি পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং ভাইভাতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করার পরও কোটা নামক ফাঁদে আটকে যেতো তার ভাগ্যের চাকা। সরকারী চাকুরীতে কোটা ছিল ৫৬%। তার বাইরে এমপি ও মন্ত্রীদের সুপারিশ এবং চাকুরীজীবি আমলাদের তদবির ছিল দৃশ্যমান।
সরকারী চাকুরীতে মেধার চেয়ে কোটার জোর ছিল বেশি। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে একটা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত রায় প্রদান করেছিল যে সরকারী চাকুরীতে কোটা কত শতাংশ থাকবে তা একান্তই সরকারের বিষয়। এখানে আদালতের রায় প্রদান করার সুযোগ নেই। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারী চাকুরীতে বিদ্যমান কোটা সংস্কারের দাবিতে শাহবাগে একটি মানববন্ধন করে কিছু তরুণ। সেই মানববন্ধন থেকে ধীরে ধীরে কোটা সংস্কার আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কোটা সংস্কার আন্দোলন এর আগেও কয়েকবার হয়েছিল। কিন্তু সরকারের দমন-পীড়নের মুখে আন্দোলনকারীরা রাজপথে টিকে থাকতে পারেনি।আমি ২০১৩ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম।ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতাদের
ব্যর্থ নেতৃত্ব , কৌশল নির্ধারণ এবং আন্দোলনের অনভিজ্ঞতার কারণে সেবার কোটা সংস্কার আন্দোলন সফল হয় নি। সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন টিকিয়ে রাখার জন্য আমি ২০১৮ সালে শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটা প্লাটফর্ম তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সবাই একেকটা নাম প্রস্তাব করলো। আমি প্রস্তাব দিলাম সংগঠনের নাম হবে “বাংলাদেশ ছাত্র পরিষদ” । একজন গণমাধ্যম কর্মী, আন্দোলনের পোড় খাওয়া এক্টিভিস্ট এবং টিভি গণমাধ্যম বিভাগের ছাত্র হিসেবে যুক্তি দিয়ে বললাম নির্দলীয় সংগঠনের নাম যত ছোট,তত ভালো। মুখস্থ করতে সুবিধা। টিভিতে গণমাধ্যম কর্মীদের ‘এনকরিং'(উচ্চারণ ) করতে সুবিধা এবং সময় কম লাগে। আমার প্রস্তাব গৃহীত এবং কৌশল তাদের কেউ গ্রহণ করে নাই।
আমি আন্দোলনের কর্মসূচি,কৌশল এবং সময় ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের সাথে একমত ছিলাম না। বললাম তাদের পদ্ধতিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে অনেক মায়ের বুক খালি হবে, শিক্ষার্থীদের রক্তের স্রোত এবং ঘামের দুর্গন্ধ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়বে। বছরের প্রথম ছয় মাসে আন্দোলনের মুখে পড়াশোনা ব্যাহত হবে। কিন্তু দাবি আদায় হবে না। সরকার যদি একান্তই বাধ্য হয় তাহলে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে অথবা নভেম্বর মাসের শুরুতে এই দাবি মেনে নেয়ার সম্ভাবনা আছে। তবুও
তারা “বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ” নামক লম্বা নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।যত দিন যাচ্ছে ততই আমার কথা গুলো সত্যি সত্যি প্রতীয়মান হচ্ছে। আমি একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে দূর থেকে দেখছি। নিউজ করে যাচ্ছি। সেই বছর ৮ এপ্রিল শাহবাগে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতাকর্মীদের উপর পুলিশের নির্মম নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যর্থতার পর আমার কথা তাদের মনে ‘কমন’ পড়ছে। নেতাদের অনুরোধে পর্দার আড়ালে আইন, আদালত এবং গণমাধ্যমে কোটা সংস্কার আন্দোলনের জন্য একজন নীরব সহযোদ্ধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। সেই বছর ৩০ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে নুরুল হক নুরের উপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলার ঘটনায় সবাই পালিয়ে গেলেও আমি ‘ঢাল’ হয়ে তাকে রক্ষা করে লাইব্রেরীর ভেতরে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কর্মরত সাংবাদিকদের নুরুল হক নুরের রক্তাক্ত শরীরের ছবি এবং তথ্য পাঠালাম। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লাইব্রেরীয়ান অধ্যাপক ডক্টর জাবেদ স্যারের গাড়িতে তোলার সময় আমার উপর নেকড়ে বাঘের মত ঝাপিয়ে পড়ল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এরপর আমাদের স্থান হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলা এবং পুলিশের অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ নেতা ও কর্মী মাঠ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর মাঠে নামার কেউ নেই। সেই আটক নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং কোটা সংস্কার আন্দোলন সফল করতে আমার ডাক পড়ে। আমি সেই ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে সংঘটিত বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার কথা বললাম নেতৃবৃন্দের কে। কারাগারে আটক নেতাকর্মীদের সঙ্গে দেখা করে ‘অভয়’ দিয়ে এসেছি। তাদের খাওয়া,থাকা এবং পরীক্ষার বিষয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা করেছি।
আমি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলাম যাতে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ব্রিফিং করে তাদের কে দিয়ে সরকার কে ঠান্ডা করতে পারি। উচ্চ আদালতের সিনিয়র আইনজীবীদের প্রেস ব্রিফিং করে আইনী লড়াই এবং প্রশাসনিক হর্তাকর্তাদের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছি। সরকার কে আল্টিমেটাম দিয়ে কারাগারে আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবি বাস্তবায়ন করেছি । অবশেষে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আমাদের ‘আংশিক ‘দাবি বাস্তবায়ন হয়েছে। আমি পুরো দাবি বাস্তবায়ন করার জন্য “সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ” গঠন করে আন্দোলন সফল করতে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু অনেক নেতাই আমার কথা শুনে নি। আমার কাছে মনে হয়েছে কোটা সংস্কার আন্দোলনের কোন কোন নেতা সরকারের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে ‘আংশিক দাবির সফলতা’ নিয়ে আমাদের মাঠ ছেড়ে চলে আসতে হলো।
কোটা সংস্কার আন্দোলন আংশিক সফলের পর আমরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম।২০১৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর আমরা ৫ দফা দাবিতে ‘নিরাপদ বাংলাদেশ চাই’ আন্দোলন শুরু করি।ঐ সময় আমার পরীক্ষা চলছিল। তবুও পরীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে আন্দোলনের সমর্থনে লিফলেট বিতরণ করেছি। পরীক্ষার পরদিন ২৩ ডিসেম্বর বিকেলে ছিল আমাদের প্রথম কর্মসূচি। দুপুরে টিএসসিতে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের নজরদারিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছিল মাঠে নামার আগেই। আমি টিএসসিতে না খেয়ে সূর্যসেন হলের সামনে ক্যাফেটেরিয়াতে খেতে আসলে আমার উপরেও এলোপাথাড়ি হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। কথা ছিল আমরা হামলা শিকার হলে আমাদের প্রথম শ্রেণীর চারজন নেতা আন্দোলনের হাল ধরবে। সরকারের সাথে আঁতাত করে তারা আন্দোলনের মাঠে আসে নি। ফলে আন্দোলন এখানেই ব্যর্থ হয়। আমরা সুস্থ হওয়ার আগেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় চলে আসে। ফলে আমাদের রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।
বাংলাদেশে অতীতে সামাজিক আন্দোলন রাষ্ট্রের এবং সমাজের পরিবর্তনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আজ রাজনৈতিক দুষ্টু চক্রের হাতে বন্দী হয়ে গেছে। সরকারের দমন – পীড়নের মুখে আন্দোলনকারীরা রাজপথে টিকে থাকাটাই চ্যালেঞ্জ। এ অবস্থায় জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে শাসক দল ও তাদের মিত্রদেরকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। প্রয়োজনে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী এবং নির্বাচনে সমর্থনকারী দেশি-বিদেশি শক্তির ব্যবসায়িক পণ্য বর্জন করতে হবে।
যেসব বিষয়গুলো নিয়ে সামাজিক আন্দোলন হতে পারে সেগুলো ব্যাখ্যা করছি।
১)নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার: একসময় বাংলাদেশের নির্বাচন মানেই ছিল সার্বজনীন উৎসব। নির্বাচন আসলেই ধনী-গরীব, শিক্ষিত -অশিক্ষিত, ক্ষমতাধর -ক্ষমতাহীন একে অপরের সাক্ষাৎ পেত। সেই ২০১৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশে এখন নির্বাচন মানেই রক্তের স্রোত, লাশের মিছিল এবং চোখে-মুখে আতঙ্ক। ভোটার সংগ্রহ পদ্ধতি থেকে ভোট গণনা পদ্ধতি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ। জীবিত ব্যক্তিরা ভোট দিতে পারে না। অথচ মৃত ব্যক্তির ভোট কাস্টিং হয়েছে বিগত কয়েক বছরের নির্বাচনগুলোতে।
এমত অবস্থায় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নাই।
বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা দুই স্তরে বিভক্ত–
ক)জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং
খ)স্থানীয় সরকার নির্বাচন।
ক) সমানুপাতিক পদ্ধতিতে(Propotional System) জাতীয় সংসদ নির্বাচন:
বিগত কয়েক বছর ধরে জোটগতভাবে নির্বাচন করায় সংসদ নির্বাচনে সহজেই সরকারি দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায়। ফলে সরকারী দল নিজেদের ইচ্ছামত আইন পাস করে এবং নিজেদের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে ।যেমন বিএনপি সরকারের আমলে নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতির বয়স বৃদ্ধি। অপরদিকে আওয়ামী লীগ আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের অধীনে নির্বাচন করে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেছে।
সংসদে সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের সংখ্যা এবং আধিপত্য কমাতে বিদ্যমান ‘সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ’ পদ্ধতির বিপরীতে ‘সমানুপাতিক’ পদ্ধতি চালু হলে জনগণের প্রতিটি ভোটের মূল্যায়ন হবে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বাড়বে।
বর্তমান পৃথিবীতে ১২২টি গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ৮৭ টি দেশে সমানুপাতিক পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন সমানুপাতিক পদ্ধতি দরকার :
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বলে স্বীকৃতি দেয়া হয় এরশাদের পতনের পর অনুষ্ঠিত ১৯৯১ সালের ৫ম সংসদ নির্বাচন কে। জাতীয় সংসদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে সেই ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৩০.৮৭ শতাংশ , যেখানে তাদের আসন ছিল ১৪০টি যা মোট আসনের ৪৬ শতাংশ। অপরদিকে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোটের হার ৩০.০৮ শতাংশ, যেখানে তাদের আসন সংখ্যা ছিল ৮৮টি যা মোট আসনের ২৯ শতাংশ। বাংলাদেশের সর্বশেষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছিল ২০০৮ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। সে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ভোট পেয়েছিল ৪৮.৯০ শতাংশ যেখানে তাদের আসন সংখ্যা ছিল ২৩০ টি যা মোট আসনের ৭৬.৬৬ শতাংশ। বিএনপি এবং জামায়াতের ভোট পেয়েছিল ৩৭.২০ শতাংশ। কিন্তু আসন সংখ্যা ছিল ৩২ টি। মা মোট আসনের ১০.৬৬ শতাংশ। (বিস্তারিত: সংস্কার সংলাপ- অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ)। আমার জানামতে,
পরে নোয়াখালী -১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বিজয়ী হওয়ার কারণে ১ টি , উচ্চ আদালতের রায়ে টাঙ্গাইল সদর আসনে বিএনপির প্রার্থী কে বিজয়ী ঘোষণা এবং হবিগঞ্জ -১ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হওয়ার কারণে বিএনপির মোট ৩ টি আসন বেড়েছে।সব মিলিয়ে সংসদে মোট আসনের সংখ্যা ছিল ৩৫ টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের দিক থেকে সরকারী দল এবং বিরোধী দল কাছাকাছি হলেও “পদ্ধতিগত” ভুলের কারণে আসন সংখ্যার ব্যবধান অনেক।
খ) দলীয় প্রতীক ছাড়াই স্থানীয় সরকার নির্বাচন:
উন্নত বিশ্বের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে স্থানীয় সরকার থেকে বেশী নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তাই উন্নত বিশ্বে স্থানীয় সরকার অনেক বেশী পাকাপোক্ত। বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিরা জনগণের বিভিন্ন বিরোধ, দ্বন্দ্ব ,সমস্যা এবং জটিলতার অবসান ঘটিয়ে শহুরে এবং গ্রামীণ জনপদে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচনের পর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। জনগণের লক্ষ লক্ষ ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সেই ২০১৩,২০১৪ এবং ২০১৫ সালে বিএনপি -জামাতের আন্দোলনে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মিথ্যা মামলায় চার্জ শিট দিয়ে শত শত জনপ্রতিনিধিকে স্থানীয় সরকারের শীর্ষ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে শাসকদলের নিজেদের পছন্দমত ব্যক্তিকে বসিয়েছে। অনেকেই উচ্চ আদালতে মামলা করে তাদের দায়িত্ব ফিরে পেয়েছেন।
সর্বোপরি,শাসকদলের সমর্থক এবং অনুগত ব্যক্তিকে স্থানীয় সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে বসানোর জন্য ২০১৫ সালে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের প্রতিটি পদে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিবাদের মুখে শহরের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব গ্রামীণ শান্তির জনপথ কেও অস্থিতিশীল করতে পারে এই আশঙ্কায় সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে (সিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর/ ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ডে মেম্বার) দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সরকার। তবে শীর্ষপর্যায়ে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য আইন পাস করেছে সরকার।
দলীয় হানাহানি, মারামারি এবং রাজনৈতিক কোন্দল এতটাই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে এখন গ্রামে এবং শহরে সামাজিকভাবে সম্মানীত ব্যক্তিরা মান সম্মান ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে প্রার্থী হওয়া তো দূরের কথা, ভোট দিতে পর্যন্ত যায় না।
তাই স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন ব্যবস্থা বাদ দিতে হবে।
পেশাজীবীদের নির্বাচনে মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশন বাদ দিতে হবে:
বাংলাদেশের এখন শুধু জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন নয় বরং পেশাজীবীদের নির্বাচনেও পাইকারি হারে ভোট ডাকাতি হচ্ছে।কয়েক বছর ধরে আইনজীবীদের সংগঠন ঢাকা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন, গাজীপুর বার এসোসিয়েশন নির্বাচন থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন পর্যন্ত ভোট ডাকাতির জঘন্য নজির স্থাপিত হয়েছে। মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশন বাদ দিয়ে দল নিরপেক্ষ
আইনজীবীদের নিয়ে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করে এসব নির্বাচনে স্বচ্ছ ও টেকসই পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ এবং ভোট গণনা পদ্ধতি নিয়ে একটা গবেষণা করতে হবে। ফলে পেশাজীবীদের নির্বাচনে আস্থার পরিবেশ ফিরে আসবে। এখানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে জায়েদ খান এবং নিপুনের দ্বন্দ্ব আদালত পর্যন্ত গড়ানোর বিষয়টাও পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে।
২) দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা: পৃথিবীর যেসব দেশে দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে , সেই সব দেশ রাজনৈতিকভাবে অধিক স্থিতিশীল। তাদের অর্থনীতি অনেকটা মজবুত। সামাজিক শৃঙ্খলা উন্নত।
পৃথিবীতে দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট রাষ্ট্র আছে ৮৭ টি। এসব দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নীতির প্রয়োগ
সত্যিকার অর্থেই কার্যকর। বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেই সংসদের নিম্নকক্ষ এবং উচ্চকক্ষ গঠন করা যেতে পারে।
ক) নিম্ন কক্ষ (জাতীয় সংসদ) : এই সভার সদস্যরা ‘জাতীয় সংসদ সদস্য’ নামে পরিচিত হবে।পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা আইনসভার নিম্ন কক্ষ গঠিত হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের সমানুপাতিক হারে আসন বিন্যাস করা হবে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে আসন সংখ্যা ৩০০টি। কোন রাজনৈতিক দল যদি সংসদে ৪০ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে সেই দল আসন ভাবে ১২০ টি। কোন রাজনৈতিক দল ১%ভোট পেলেও আসন পাবে ৩ টি আসন পাবে। সর্বনিম্ন .৩৪% ভোট পেলেও একটি আসন পাবে।
১)এখানে প্রশ্ন আসতে পারে রাজনৈতিক দল গুলো কোন ব্যক্তিকে সংসদে মনোনয়ন দিবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনের তৃণমূল পর্যায় থেকে যেসব ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হবে ,সেসব ব্যক্তিকেই মনোনয়ন দেয়া হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দলগুলো সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গোয়েন্দা সংস্থার জরিপের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে থাকে।
২) বাংলাদেশের জনগণ শুধুমাত্র দলকে ভোট দেয় না, ব্যক্তি দেখেও ভোট দেয়। বর্তমান ভোট গ্রহণ পদ্ধতিতে দলের ভোট এবং ব্যক্তির ভোট পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। এজন্য একই দিনে একসাথে ব্যক্তি এবং দলের পৃথক ব্যালট পেপার দিয়ে ভোটগ্রহণ হলে ব্যক্তি এবং দলের ভোট হিসাব করতে সুবিধা হবে। ব্যক্তি এবং দলের ভোট মিলিয়ে প্রাপ্ত স্কোর অনুযায়ী সংসদে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা নির্বাচন কমিশনের গেজেটে প্রকাশ করা হবে।
৩) কোন সংসদ সদস্য মারা গেলে ঐ আসনে উপনির্বাচনের নিয়ম রয়েছে বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থায়। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মারা গেলে উপনির্বাচন হবে ঠিকই। তবে সেটা মাত্র ব্যক্তির ব্যালট পেপারে ভোট হবে। দলীয় ভোটের এর প্রয়োজন নেই। তবে গেজেট প্রকাশের ক্ষেত্রে দলীয় প্রাপ্ত ভোট এবং ব্যক্তির প্রাপ্ত ভোট হিসাব করা হবে।
নিম্নকক্ষ আইন প্রণয়ন করবে। নিম্ন কক্ষে পাসের পর সেই আইন উচ্চকক্ষের সদস্যদের ভোটে অনুমোদিত হতে হবে।
খ) উচ্চ কক্ষ (জাতীয় পরিষদ): এই সভার সদস্যরা ‘জাতীয় পরিষদ সদস্য’ নামে পরিচিত হবে। এটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট হলে সবচেয়ে ভালো হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে
উচ্চ কক্ষে আসন বিন্যাস হবে। তাদের কোন দলীয় পরিচয় থাকবে না। রাষ্ট্রপতি হতে গেলে যেমন কোন এমপিকে দলীয় পদ এবং সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়, তেমনি উচ্চ কক্ষের
আসনে নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে দলীয় ও নিম্নকক্ষের সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। উচ্চ কক্ষের সদস্যদের পদমর্যাদা বেতনবার্তা এবং অন্যান্য সুবিধাবি নিম্ন কক্ষের সাথে কখনো কম হবে না।
উচ্চ কক্ষের উপদেশমূলক এখতিয়ার এবং ভেটো দেওয়ার এখতিয়ার থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া
নির্বাচন কমিশন সহ সমস্ত সাংবিধানিক পদের নিয়োগ উচ্চ কক্ষের সদস্যদের অনুমোদিত হতে হবে।
৩)উচ্চ কক্ষ থেকে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন:
বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক সহিংসতার উদ্ভব হয় মূলত নির্বাচন কে ঘিরে।
প্রতি পাঁচ বছর পর যখন নির্বাচন আসে , তখন নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিভেদ এবং মতপার্থক্য দেখা যায়। কেউ দলীয় সরকার , কেউ নির্দলীয় এবং নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার, কেউ আবার নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার এবং কেউ আবার জাতীয় সরকারের দাবি করে থাকে। ১৯৯৬ সালের মার্চে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে পাস হওয়া ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারের’ পদ্ধতিতে আইনগত দিক থেকে কিছু ভুল -ত্রুটি- বিচ্যুতি ছিল। সেই সব ভুল- ত্রুটি -বিচ্যুতি দূর করলেই একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা যেত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট করার পর উচ্চ আদালত সেই সব ভুল -ত্রুটি -বিচ্যুতি চিহ্নিত করে তা সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে পারতো।তা না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করাটা “অসুস্থ রোগীর চিকিৎসা না করে রোগীকে ইনজেকশন পুশ করে মেরে ফেলার মত”।
নির্বাচনকালীন সরকারের দাবির নাম যেটাই হোক না কেন, নির্বাচনকালীন সরকার হতে হবে দলীয় প্রভাব মুক্ত এবং জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত যাতে সংবিধানের মূলনীত “গণতন্ত্র” এর চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।
যেহেতু উচ্চ কক্ষের সদস্যদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় থাকবে না এবং তারা জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত সেহেতু উচ্চ কক্ষের সদস্যদের দ্বারাই নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা হবে। নির্বাচনের আগে নিম্নকক্ষ অবশ্যই ভেঙে দিতে হবে। সংসদের উচ্চ কক্ষের সদস্যরা জনগণের ম্যান্ডেড প্রাপ্ত সকল সংসদীয় রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নির্বাচিত হবেন বিধায় তাদের চেয়ে “সর্বদলীয় জাতীয় সরকার” আর হতে পারে না।
প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ: ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং মেট্রোরেল চালুর পরও ঢাকা শহরে যানজট নিরসন হয়নি। কারণ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ প্রশাসনিক এবং
বিচারিক কাজের জন্য ঢাকা শহরে আসছে।
কাজেই নাগরিক সুযোগ সুবিধা জনগণের দ্বার গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রশাসনিক এবং বিচারক সহ বিভিন্ন কাজের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।যেমন- শাহবাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য সারাদেশ থেকে রোগীরা এসে ভীড় জমায়। তাই বিভাগীয় শহরগুলোতে হয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে অথবা বিভাগীয় শহরে শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা চালু করতে হবে।
৫) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা:
বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন”। দীর্ঘদিন ধরে এই নীতির বাস্তবায়ন না হওয়ায় মাসদার হোসেন নামে একজন বিচারক হাইকোর্ট রিট করেন।
ঐতিহাসিক মাসদার হোসেন মামলায় উচ্চ আদালত বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের জন্য রায় প্রদান করেন। ১/১১ তে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালের ১নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রায় বাস্তবায়ন হয়। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ করে থাকেন। ফলে বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে স্বাধীন বিচার বিভাগ এখনো অধরাই থেকে গেল। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নয় বরং উচ্চ কক্ষের সদস্যদের পরামর্শক্রমে এবং অনুমোদনে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের উচ্চ আদালতের কয়েকজন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি অবসরে যাওয়ার সময় বিচারপতি ‘নিয়োগ আইন’ প্রণয়নের কথা বলেছেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিচারক নিয়োগের জন্য একটি আইন থাকা দরকার। পাশাপাশি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ‘আইন ও বিচার বিভাগ কে পৃথক করে ‘স্বাধীন বিচার বিভাগ’ প্রতিষ্ঠায় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটা বিচার বিভাগীয় সচিবালয় থাকা উচিত।
বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে ভৌগোলিক দুরত্ব,জনসংখ্যা, মামলার সংখ্যা অনুযায়ী আদালত স্থাপন করতে হবে। মামলার সংখ্যা এবং ধরন অনুযায়ী বিচারক নিয়োগ দিতে হবে। এজন্য
ঢাকার বাহিরে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপন করা উচিত।
(চলবে)
লেখক: গণমাধ্যম কর্মী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক।